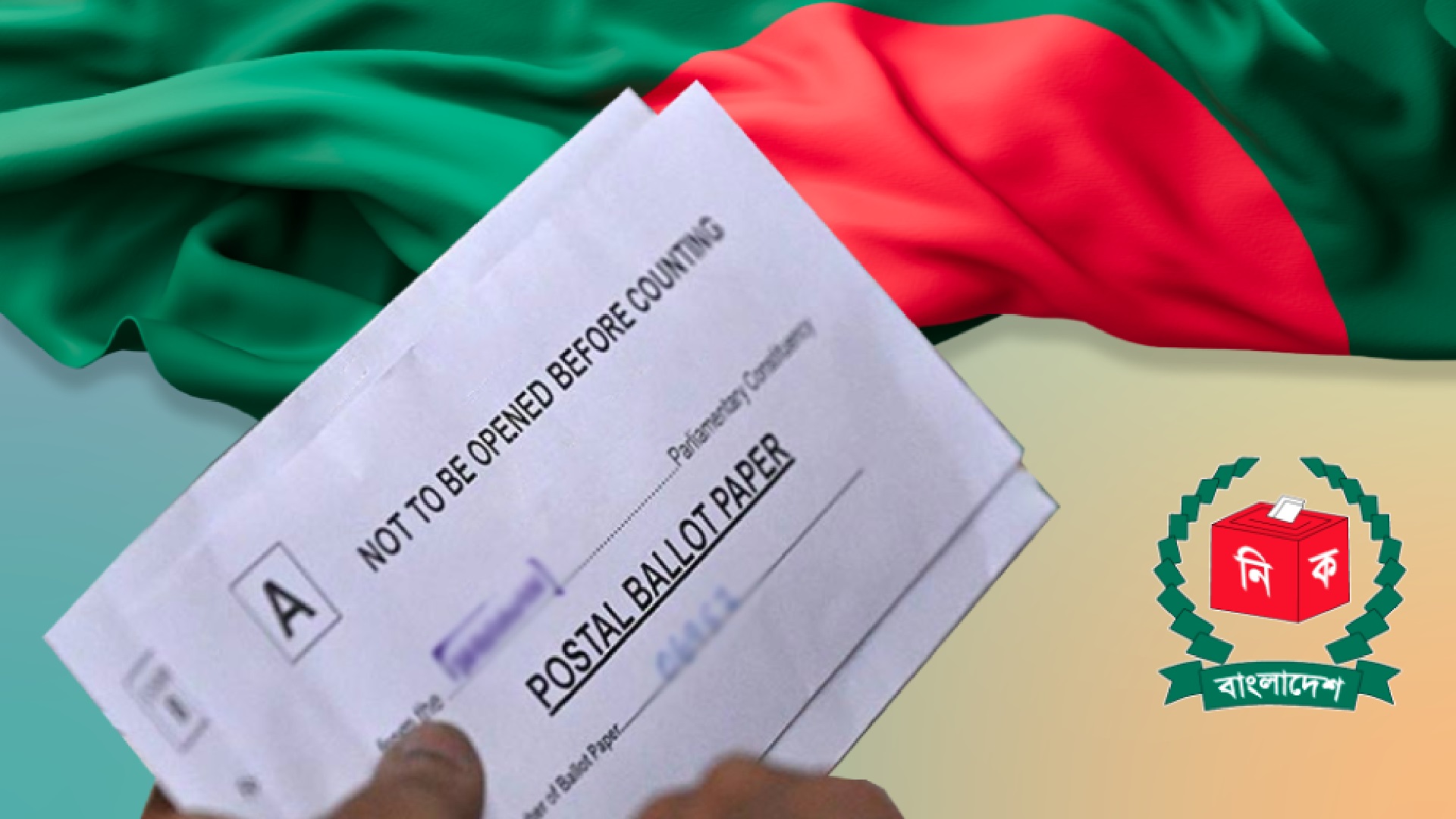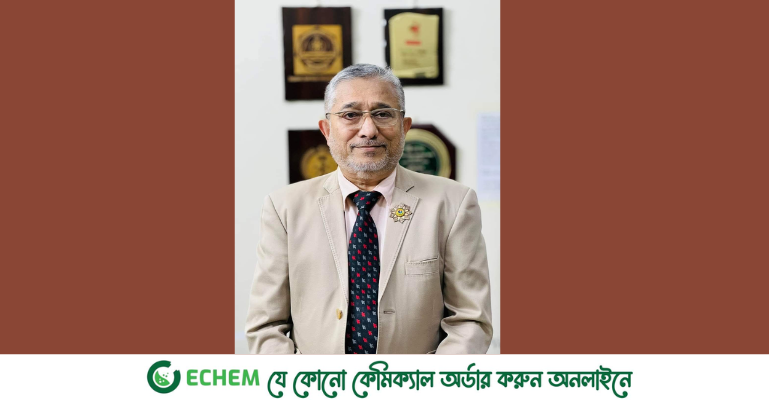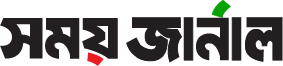সময় জার্নাল প্রতিবেদক:
দেশের নানামুখী সংস্কার, জনগণের মৌলিক অর্থনৈতিক, নাগরিক অধিকার বাস্তবায়ন ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে বৈষম্যহীন দেশ গড়া, দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশের বিনিয়োগ স্থবিরতা কাটেনি, রাজনীতির সংস্কার ও বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা দূর করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি সরকার। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি ও বেকারত্ব তো রয়েছেই। সরকার গঠনের পর ১০ মাসে পেরিয়ে গেলেও টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করছে দেশে। তবে সুনির্দিষ্ট কোন সংস্কার দেখা যায়নি। দেশের মানুষের মাঝে স্বস্থি ফেরাতে দরকার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা।
আর এই দেশ গড়তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছেন জিওপলিটিক্যাল ইকোনমিস্ট অধ্যাপক সৈয়দ আহসানুল আলম পারভেজ। 'বাংলাদেশে একটি জনবান্ধব সমাজ ও অর্থনীতি বাস্তবায়নের প্রস্তাবনা' বইতে অধ্যাপক পারভেজ তথ্য নির্ভর বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার রূপরেখা তুলে ধরেছেন।
আজকের লেখায় অধ্যাপক পারভেজের রুপরেখার চতুর্থ পর্ব-
ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, নারী ও স্টার্ট আপের জন্য ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (এসএমই) বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলেও, অর্থায়ন পেতে প্রায়ই নানা বাধার সম্মুখীন হয়। তথ্য অনুযায়ী, এমএসএমই খাতে বর্তমানে ২.৮বিলিয়ন ডলারের আর্থিক ঘাটতি রয়েছে এবং নারী পরিচালিত এসএমই-এর ৬০% ঋণ চাহিদা অপূর্ণ (৩৫)। নারীরা এখন দেশের মোট ব্যবসার প্রায় ১০-১২% পরিচালনা করছে (২০১৩সালের ৭.২%-এর তুলনায় উন্নতি হলেও), তবে তারা ব্যাংক ঋণের খুব সামান্য অংশ পাচ্ছে। উচ্চ জামানত চাহিদা ও পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে নারী উদ্যোক্তা এবং তরুণ স্টার্ট আপরা প্রায়ই ঋণ প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হয়। এই প্রস্তাবনাগুলো ঋণ কাঠামোসহজীকরণ এবং এই গোষ্ঠীগুলোর জন্য বিশেষ ঋণ সহায়তার আহবান জানায়।
বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যেমন, ২০২৩সালে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্প সুদের (৫%) রিফাইন্যান্স স্কিম চালু করেছে এবং ব্যাংকগুলোকে নারী উদ্যোক্তাদের কাছে ঋণ দিতে উৎসাহিত করেছে। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, প্রস্তাবনাগুলো নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ঋণ সংস্থান, নারীদের জন্য জামানতমুক্ত বা গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ প্রদান এবং গ্রামীণ এসএমই-এর জন্য সহজ ঋণ প্রক্রিয়া চালুর সুপারিশ করে। বর্তমানে এসএমই-র প্রায় ৪৬% ঋণ পেতে সক্ষম হয়েছে, অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি এখনো বঞ্চিত।
ব্যাংকগুলোর জন্য এসএমই খাতে (বিশেষ করে ঢাকা-চট্টগ্রামের বাইরে) আরও বেশি ঋণ বিতরণের বাধ্যবাধকতা আরোপ এবং তরুণ উদ্ভাবকদের জন্য কোটা নির্ধারণের মাধ্যমে ছোট ব্যবসার বিকাশ ত্বরান্বিত করা হবে। বিশেষভাবে নারী উদ্যোক্তারা, যারা এক বিশাল সম্ভাবনাময় জনশক্তি, এতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। সংক্ষেপে, সরকার-বেসরকারি তহবিল, স্বল্প সুদের স্কিম এবং ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধার মাধ্যমে এসএমই ওস্টার্ট আপের জন্য ঋণ প্রাপ্তির পথ সহজ করে এই নীতিমালা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে শক্তিশালী করবে।
কৃষিশিল্প এবং গ্রামীণ ঋণ সহায়তা
বাংলাদেশের মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৪৫% কৃষিতে নিয়োজিত এবং কৃষিখাত দেশের জিডিপি-র ১১% অবদান রাখে, তবুও কৃষক এবং কৃষিশিল্পগুলো আনুষ্ঠানিক ঋণের খুব অল্প অংশ পেয়ে থাকে (৩৬)। ২০২৩ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহ প্রায় ৩২৮বিলিয়ন টাকা কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ বিতরণ করেছে (৩৬), যা লক্ষ্য পূরণ করেছে কিন্তু এটি মোট ব্যাংক ঋণের মাত্র ২.৫-৩%। আসলেই, বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের ঋণ পোর্টফোলিওর ২% এরও কম কৃষি খাতে বিনিয়োগ করে (৩৭)। (বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যূনতম ২% কৃষি ঋণ বরাদ্দের নির্দেশনা দিয়েছে)।
গ্রামীণ পরিবারের বেশিরভাগই মাইক্রো ফাইন্যান্স এনজিও বা অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতার ওপর নির্ভর করে; কৃষক পরিবারের মধ্যে যারা ঋণ নিয়েছে, তাদের ৬৩% এনজিও থেকে এবং মাত্র ২৬% ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে (৩৬)। এছাড়া, ব্যাংকগুলো সাধারণত ক্ষুদ্র কৃষকের পরিবর্তে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীকে ঋণ দিতে বেশি আগ্রহী। এই ঘাটতি দূর করতে, প্রস্তাবনাগুলো কৃষিখাত এবং কৃষি শিল্পের জন্য ঋণ প্রবাহ বাড়ানোর আহবান জানায়। বিশেষত, কৃষি এসএমই (যেমন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কোল্ড স্টোরেজ, কৃষি যন্ত্রপাতি সেবা) এর জন্য রিফাইন্যান্স স্কিম জোরদার করা এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকসহ বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ক্ষমতা বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে।
কৃষি শিল্পের ঋণে সুদ ভর্তুকি বা ক্রেডিট গ্যারান্টি চালু করলে ব্যাংকগুলোকে কৃষিখাতে আরও বেশি ঋণ প্রদান করতে উৎসাহিত করা যাবে। গ্রামাঞ্চলে শাখাবিহীন ব্যাংকিং এবং ডিজিটাল ফাইন্যান্স সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষকদের কাছে ঋণ পৌঁছানোর ব্যবস্থাও প্রস্তাবিত হয়েছে। কৃষি শিল্পের উন্নয়ন ও আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করলে শুধু গ্রামীণ আয় বাড়বেনা, বরং ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমবে এবং কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজনও হবে। এই পদক্ষেপগুলো কৃষিখাতের অর্থনৈতিক গুরুত্বের তুলনায় চলমান অর্থায়ন ঘাটতি দূর করতে এবং গ্রামীণ ন্যায়বিচার ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়ক হবে।
নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য আবাসন ও শহুরে বস্তির সমস্যা মোকাবিলা
বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের ফলে নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য আবাসন সংকট আরও তীব্র হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর ২০২৪সালের হালনাগাদ তথ্যে দেখা গেছে, বর্তমানে দেশে প্রায় ৩.৫মিলিয়ন মানুষ বস্তিতে বাস করছে যা ২০১৪সালের ২.২৩মিলিয়নের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে ঢাকায়ই রয়েছে প্রায়২.৮মিলিয়ন বস্তিবাসী, যাদেশের মোট বস্তিবাসীর ৮০%। ৭৮% বস্তির পরিবার একক কক্ষে বসবাস করে যা চরম জনাকীর্ণতার ইঙ্গিত দেয়। পাইপলাইনের পানির সুবিধা রয়েছে মাত্র ৩৫% পরিবারের এবং ৪২% পরিবারের যথাযথ স্যানিটেশন সুবিধা নেই।
গ্রাম-শহর অভিবাসন এবং জমির মূল্য বৃদ্ধির কারণে ২০১৪সালের পর থেকে অনানুষ্ঠানিক বসতির সংখ্যা ২২% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চিত্র স্পষ্টভাবে দেখায় যে, বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করতে জরুরি নীতিগত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, বিশেষ করে ঢাকায়, যেখানে ৯২% নতুন অভিবাসী অনানুষ্ঠানিক বসতিতে আশ্রয় নেয় (৩৮)। এই নীতিমালার মাধ্যমে সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প সম্প্রসারণ, বস্তি উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগণের জন্য আবাসন ঋণ সহজীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ভর্তুকি যুক্ত অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ বা বিদ্যমান বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন (পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ সংযোগ) করলে সরাসরি লাখ লাখ শহুরে দরিদ্র উপকৃত হবে, যারা এখন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উচ্চ ভাড়ায় বসবাস করে। এই প্রস্তাবনা বড় মাপের নিম্ন আয়ের গৃহায়ন ঘাটতি দূর করতে সহায়ক হবে।
এছাড়া, নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য আবাসন তহবিল বা মাইক্রো-মর্টগেজ স্কিম চালুর সুপারিশ করা হয়েছে, যাতে কেবল ধনী শ্রেণি নয়, দরিদ্ররাও গৃহস্বত্ব অর্জন করতে পারে। আবাসনের সাথে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সরাসরিযুক্ত; উন্নত আবাসন ব্যবস্থাপনা বস্তিতে রোগ ব্যাধি ও অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমাবে।
মোটকথা, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং কমিউনিটি নেতৃত্বাধীন আবাসন উদ্যোগের মাধ্যমে "সবার জন্য আবাসন" নীতির বাস্তবায়ন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সামাজিক মর্যাদায় পরিণত করতে সহায়ক হবে।
সময় জার্নাল/এমআই